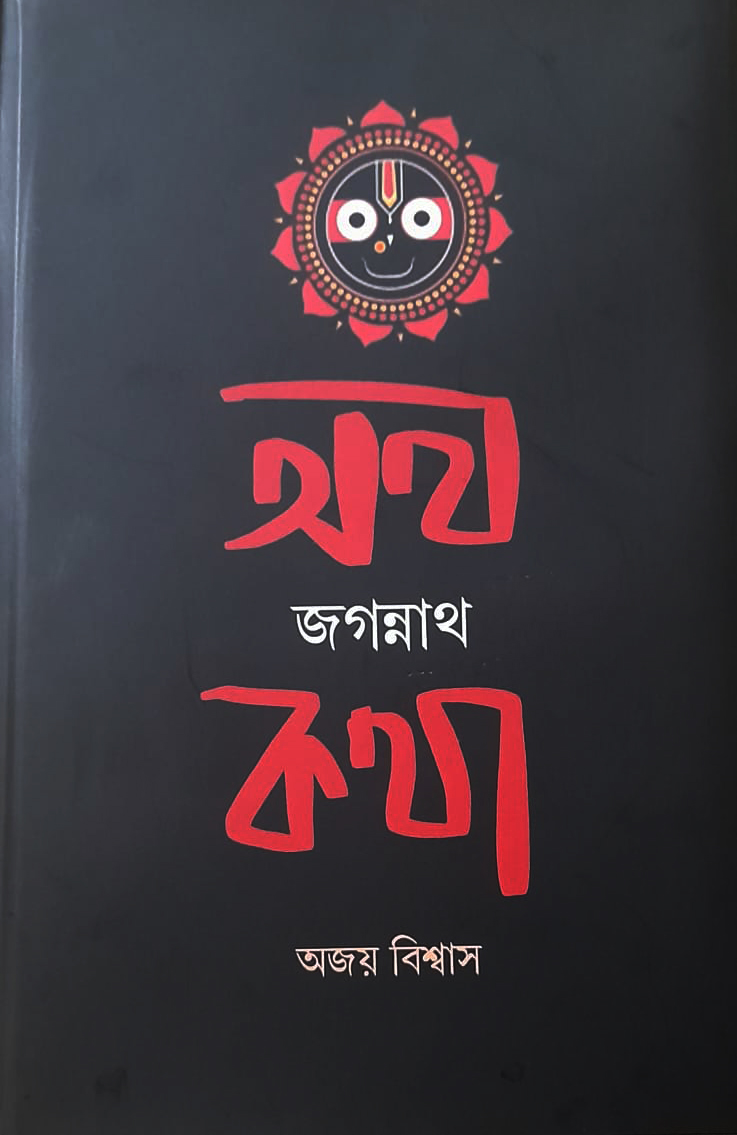ডঃ বিকাশ পাল
ডঃ বিকাশ পাল
আজ ২৫শে বৈশাখ। সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালির জীবনে অত্যন্ত গর্বের দিন। কেননা, রবীন্দ্রনাথ এই দিনটিতেই জন্মেছিলেন।
আমার ছোটবেলায় এই দিনটির অভিজ্ঞতা খুবই স্মৃতিমধুর। সকাল সকাল আমাদের বাড়ির আশেপাশের গুলঞ্চ গাছ থেকে ফুল তুলতাম। দিদি মালা বানিয়ে দিত। আর সেই মালা নিয়েই স্কুলে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে যোগ দেওয়ার জন্য দৌড় লাগাতাম– বিশেষ আকর্ষণ থাকত মুড়ি আর ছোলাসেদ্ধ। স্কুলে সেভাবে পড়ার বাইরের বই বা রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ার অভ্যাস তৈরিই হয়নি –কেউ সেভাবে বলেনওনি। এভাবেই আমার জীবনের কত গুলো বছর পেরিয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের কাব্য কর্মের সাথে পরিচিত না হয়েই। তবে দু’তিন দশক ধরে আমার চেতনার প্রায় প্রত্যেক মুহূর্ত জুড়ে তিনি। ঘরে বাইরে , দেশে বিদেশে, সজনে বিজনে, যেখানেই থাকি, তাঁর লেখা আমার সঙ্গী। এখনও তাঁর লেখার এক দশমাংশও পড়ে উঠতে পারিনি। তবে তাঁর অনেক চিঠিপত্র, প্রায় সব উপন্যাস আর ছোট গল্প, প্রবন্ধ গীতাঞ্জলি সহ আরও কিছু কবিতা পড়ে উঠতে পেরেছি ।

গত বছর এই দিনটিতে গিয়েছিলাম লন্ডনের সেই বাড়িটির সামনে, যেখানে কয়েক মাস থেকে তিনি গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদের কাজ শেষ করেছিলেন। সেটা ১৯১২ সালের জুন-জুলাই নাগাদ। এখন সে বাড়িতে তাঁর নামে একটি নীল ফলক বসেছে। সকলের জানা, তিনি তাঁর গীতাঞ্জলির জন্য নোবেল পুরষ্কার পান। তবে গীতাঞ্জলির কিছু আর তার বাইরেরও কিছু তাঁর পছন্দের কবিতা সহ মোট ১১৪টি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করে তিনি বন্ধু রথেন্সটাইন-এর হাতে দিয়েছিলেন। এর একটা সুন্দর প্রেক্ষিত আছে। আজ তাঁর জন্মদিনে বিশেষ করে মনে পড়ছে সে প্রসঙ্গ।
গীতাঞ্জলিতে এই গীতিকবিতাগুলির বক্তব্যকে চালিত করেছে তাঁর চেতনার গভীর সংবেদনশীলতা, সজীবতা আর প্রকৃতির সাথে তাঁর অস্তিত্বের একাত্মতা। কবিতাগুলির পরতে পরতে প্রতিফলিত তাঁর বিনম্রতা, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, আশা, ত্যাগ-তিতিক্ষার অনুভূতি। তিনি নিজেকে বিশ্ববিধাতার কাছে সমর্পণ করেছেন – এই বিশ্ববিধাতা আর কেউ নন – তাঁর অন্তরেই তিনি সব সময় বিরাজমান, এক সর্বশক্তিমান পরমপুরুষ যাকে তিনি অনুভব করার চেষ্টা করেছেন আজীবন। কখনো তিনি প্রভু, কখনও সখা, কখনও রাজন, আবার কখনও পরানসখা, নাথ, প্রাণনাথ, বন্ধু, মহারাজ, প্রিয়তম ইত্যাদি।
উপনিষদের বাণী তাঁর জীবনচেতনাকে চালিত করেছে প্রথম থেকেই। পিতা মহর্ষির কাছে তিনি পাঁচ বছর বয়স থেকেই নিয়মিত সকাল সন্ধে সংস্কৃত আর ইংরেজি শিখেছেন, মাঝে মাঝে হিমালয়ে সময় কাটিয়েছেন। দু বেলা উপাসনা করেছেন। জীবনবোধের ভিত এভাবেই তৈরি হয়েছে তাঁর। প্রতিভা জন্মগত। তারও বেশ কিছু পরে জমিদারির কাজ দেখাশোনার সময় বাংলার শিলাইদহ পতিসর আর সাজাদপুরে গ্রাম বাংলার পল্লি-প্রকৃতিকে, মানুষকে কাছ থেকে দেখেছেন। আর তাঁদের সাথে একাত্ম হয়েছেন। দিনের পর দিন পদ্মায় একা একা নৌকোয় দিনের আলো আর রাতের জ্যোৎস্নায় দূর নীহারিকার থেকে ভেসে আসা মহাজাগতিক তরঙ্গের কম্পনের মধ্যে প্রাণের স্পন্দনকে অনুভব করেছেন। কবিতা গান লিখেছেন।
গীতাঞ্জলির সুন্দর ১৫৮টির এমনই একটি গানের কিছুটা হল:
“এসো অঙ্গে পুলকময় পরশে,
এসো চিত্তে সুধাময় হরষে।
এসো মুগ্ধ মুদিত দু নয়ানে ,
তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে,
এসো গন্ধে বরণে, এসো গানে।”
ভাদ্রমাসের একদিন তিনি পতিসরের নদী জলা বিলের ওপর দিয়ে নৌকোয় চলেছেন তাঁর জমিদারির কাজে। বিলে ভেসে যাওয়া সবুজ কচুরি পানার ওপর সূর্যের উজ্জ্বল আলো পড়েছে। তিনি নৌকার জানালার পাশে একটি হেলান দেওয়া চেয়ারে বসে অন্য একটি চৌকিতে পা রেখে সরস শৈবালের নবীন কোমলতার ওপর তাঁর চোখ দুটির স্নেহ স্পর্শ অলসভাবে বুলোতে বুলোতে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছেন। এই অসাধারণ মুহূর্তগুলি পৃথিবীর গান হয়ে তখন তাঁর মনের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে, কত টুকরো টুকরো সুর মনে জমছে, আবার সেসব মন থেকে সরেও যাচ্ছে। তখনই গীতাঞ্জলির এই গানের কয়েকটি লাইন লিখেছিলেন। আর রামকেলির সুরে গুন গুনও করেছিলেন। পরে এটি একটি সম্পূর্ণ গানে পরিণত হয়। উপনিষদলব্ধ জীবন চেতনা আর তাঁর প্রাণের সাথে প্রকৃতির অখণ্ডতার অনুভূতির মিশেলই ছিল তাঁর গীতাঞ্জলির প্রেরণা।
১৯০৯-১৯১০ সালেই গীতাঞ্জলির কাজ শেষ করেন। আর ১৯১০ সালেই বিশ্বখ্যাত চিত্রকর উইলিয়াম রথেন্সটাইন লন্ডন থেকে ভারতে এলেন অজন্তা ইলোরার গুহাচিত্র দেখার জন্য। সেখান থেকে বেনারস। ভাইপো অবনীন্দ্রনাথের একান্ত অনুরোধে তিনি কোলকাতায় এলেন কোলকাতা আর্ট সোসাইটির সদ্যস্যদের সাথে কিছুদিন সময় কাটাতে। সেই সময় অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে একদিন শান্তিনিকেতনে নিয়ে এলেন। এভাবেই রবীন্দ্রনাথের সাথে উইলিয়াম রথেন্সটাইনের যোগাযোগ হল। চিত্র শিল্পী হলেও উইলিয়াম লেখালেখিও করতেন। রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির কয়েকটি কবিতা অনুবাদ করে উইলিয়ামকে পড়তে দিলেন। উইলিয়ামের ভীষণ পছন্দ হল কবিতাগুলি। লন্ডন ফিরে ‘রয়্যাল সোসাইটি অফ লিটারেচার’-এর কবি সদস্যদের শোনালেন সেসব কবিতা। সেখানে ঠিক হল আর কিছু কবিতা অনুবাদ করে কবিকে লন্ডনে আমন্ত্রণ জানানো হবে।
১৯১২ সালের জুন মাসে রবীন্দ্রনাথ বিলেতে এলেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ আর পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে। তার আগে বেশ কিছু অনুবাদ করেছেন শান্তিনিকেতন আর শিলাইদহে, কিছু জাহাজে, বাদ বাকি লন্ডনে করবেন ঠিক করলেন। উঠলেন নর্থ লন্ডনের হামসটেড হিথ গার্ডেনসের বাড়িতে – উইলিয়ামের ব্যবস্থাপনায়। দেখলেন গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি সঙ্গে নেই। অনুমান করলেন, লন্ডনের পাতাল রেলেই তাঁদের গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপির অ্যাটাচি ফেলে এসেছেন। মাথায় হাত। বাবার পরামর্শে রথীন্দ্রনাথ London Under Ground-এর lost and found property section-এ যোগাযোগ করলেন। কপাল যোগে তা পাওয়াও গেল পরের দিনই। তিনি গীতাঞ্জলি ছাড়াও তাঁর আগের লেখা কিছু কবিতা আর প্রবন্ধ ছোট গল্প অনুবাদ করেছিলেন। লন্ডনের প্রকাশনা সংস্থা Mac Millan Company তার কিছু কিছু টাইপ করে কবিকে দিল।
রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার কবি – তাই তাঁকেও রয়্যাল সোসাইটি অফ লিটারেচার-এর সদ্যস্যরা নোবেল পুরস্কারের জন্য যাতে বিবেচনা করেন, সেজন্য উইলিয়াম সহ , যাঁদের গীতাঞ্জলির অনুবাদ ভালো লেগেছিল তাঁদের অনেকেই চেষ্টা চরিত্র করলেন। ১০০ জন সদস্যের মধ্যে ৯৭ জন সদস্য Thomas Hardyকে মনোনয়নের জন্য সমর্থন করেন। মাত্র যে ১ জন সমর্থন করেন রবীন্দ্রনাথকে। তিনি ইংল্যান্ডেরই অন্য এক কবি থমাস মুর (Thomas Moore)। ব্রিটেন থেকে Thomas Hardy কে মনোনয়ন দেওয়া হয় সে বছর। Thomas Moore সেই সিদ্ধান্তে খুশি হননি । তাই তিনি সরাসরি নোবেল ফাউন্ডেশনে রবীন্দ্রনাথকে একক ভাবে মনোনয়ন করেন। সে বছর মোট ২৮ জনের মনোনয়ন জমা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হলেন। এর পরেও Thomas Hardy প্রায় ১২ বারের মত মনোনীত হন – কিন্তু নোবেল পুরস্কার তাঁর অধরাই থেকে যায়। নোবেল কমিটির এক প্যানেল সদস্যের কথায় ‘no poet in Europe, since the death of Goethe in 1832 can rival Tagore’। তারপর রাতারাতি তিনি হয়ে উঠলেন বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত মানুষ। তিনি গীতাঞ্জলি কিন্তু লিখেছিলেন দেশের মানুষের জন্য। তাই লিখেছিলেন, “পূর্বের দেবতার জন্য যে পূজার অর্ঘ্য সাজিয়েছিলাম, তা পশ্চিমের দেবতা গ্রহণ করল।”
ভারতে নোবেল পুরস্কারের খবর পৌঁছতে কয়েকদিন দেরি হয়। নোবেল ফাউন্ডেশনের কাছে যে ঠিকানা Thomas Moore উল্লেখ করেন, তা হল লন্ডনের Mac Millan Company-র। তাই টেলিগ্রাম লন্ডন হয়ে বোলপুরে পৌঁছয় কয়েকদিন পর। সেদিন রবিঠাকুর কয়েকজন অতিথিকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের আশেপাশের শাল পিয়াশালের বনে। টেলিগ্রামে একটু চোখ বুলিয়েই পকেটে রেখে দেন। পরে পোস্টমান বলেন, কর্তা ওটা ভাল করে দেখুন, বড় খবর আছে। তখন ভ্রমণ সঙ্গীদের জেদাজেদিতে ভালো করে পড়লেন – কিন্তু অবিশ্বাস্য এই খবরটা নিজে দিতে চাইলেন না – এটা তাঁর বিনম্রতার পরিচয় – শুধু কবিতাতেই নয় – জীবনেও। আবেগহীন ভাবে ছেলে রথীর হাতে দিলেন – তার পর যখন শান্তিনিকেতনে সন্ধ্যাবেলায় ফিরলেন, তখন সেখানে লোকে লোকারণ্য। আর সারা বাংলায় এই খবর দাবানলের মত হু হু করে ছড়িয়ে পড়ে। তিন চার দিন সকলের অভিনন্দনের উত্তর দিতে সময় গেল – তাও ছাপানো উত্তর। তিনদিন পরে বন্ধু উইলিয়ামকে ধন্যবাদ জানালেন চিঠি লিখে – যার কিছুটা এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক।
“The very first moment I received the message of the great honour conferred on me by the award of the Nobel Prize my heart turned towards you with love and gratitude. I felt certain that of all my friends none would be more glad at this news than you. But, all the same, it is a very great trial for me. The perfect whirlwind of public excitement it has given rise to is frightful. It is almost as bad as tying a tin can to a dog’s tail, making it impossible for him to move without creating noise and collecting crowds all along. I am being smothered with telegrams and letters for the last few days and people who have never read a line of my works are loudest in their protestations of joy. I cannot tell you how tired I am of all this shouting, the stupendous amount of its unreality being something appalling. Really, these people honour the honour in me and not myself…” Excerpted with permission from Daughters of Jorasanko, Aruna Chakravarti, HarperCollins India.
নোবেল পুরস্কারের এই জগৎজোড়া খ্যাতি রবীন্দ্রনাথকে নিভৃত অবসর থেকে অনেক দূরে নিয়ে গেল। সারা পৃথিবী থেকে ডাক আসতে লাগল বছরের পর বছর। সে সব ভ্রমণের খুঁটিনাটি খুব অল্পই আমার পড়া হয়েছে। তাও যতটুকু পড়েছি, সেটা লিখতে গেলেও অনেক পাতা হবে। শুধু দু চারটি ঘটনাতেই পরিস্কার হয়ে যায়, তিনি তখন খ্যাতির কোন শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। সত্যিই তিনি তখন এশিয়ার শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি ।
ইন্দোনেশিয়ার জাভার সূর্যকর্তা রাজ্যের রাজার অনুরোধ রাখতে গিয়ে দেখলেন – রাজনগরীতে তাঁকে একটি সেতু সহ রাস্তা উদ্বোধন করতে হল – যার নাম জালান (রোড) টেগোর। ইতালির প্রেসিডেন্ট মুসৌলিনি নিজের সমালোচিত ভাবমূর্তির পরিবর্তনের জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন রোমে আসার। তিনি সেই ফাঁদে পাও দেন। ইরানের রেজা শাহ পল্লভি তেহরানের সংসদ ভবনে ১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথকে নাগরিক সম্বর্ধনা দেন – সেই সঙ্গে ৭ মে ইরানের সরকার তাঁর জন্মদিন পালন করে। পারস্যের চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন – ‘এই প্রথম কোন রাষ্ট্র তাঁর জন্মদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে পালন করল’, সেদিন তাঁর মনে হয়েছিল তাঁর পুনর্জন্ম হয়েছে। তিনি দ্বিজ। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্বর্ধনা দিল। সেখানে সারাদিন একটি কর্মশালায় তিনি বক্তব্য রাখলেন, যেটি পরে Sadhana – The realisation of life বলে বই হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। হার্ভার্ড বক্তৃতায় যে রবীন্দ্রনাথকে পাই, তিনি কবিতা, গান, বা গল্পের রবীন্দ্রনাথ নন, তিনি ঋষি রবীন্দ্রনাথ। রাশিয়ার চিঠিতে আমি যে রবীন্দ্রনাথকে পাই, তিনি সমাজবিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ। আবার ছুটি, কাবুলিওয়ালা, দেনা পাওনা, পোস্ট মাস্টার – এই সব গল্পে তিনি মানুষ রবীন্দ্রনাথ।
তবে সম্মানের সাথে সাথে ভারতবর্ষে কেন, শুধু দুই বাংলাতেই অনেক রবীন্দ্রসমালোচনাও হয়েছে, নোবেল পাওয়ার আগে ও পরে।
গিরিশ কারনাড একবার বলেছিলেন, “Tagore is a great poet but a second-class playwright.” আমার ধারণা, উনি যদি শুধু মন দিয়ে ‘তাসের দেশ’ বা ‘রক্তকরবী’ নাট গুলো দেখতেন, তাহলে এই ধরনের মত প্রকাশ করতেন না। ২০২৩ এর ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয়-সামাজিক পটভূমিতেও এই নাটক গুলির বার্তা কত প্রাসঙ্গিক।
কল্লোল যুগের বিখ্যাত কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর ‘সাগর থেকে ফেরা’ কাব্য গ্রন্থে একটি কবিতায় লিখেছিলেন।
‘জল পড়ে পাতা নড়ে
এই নিয়ে পদ্য,
লিখে ফেলে ভাবলাম
হল অনবদ্য।”
পরে তিনি এই কাব্য গ্রন্থেরই জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পান। তাঁর জীবনের শেষের দিকে একবার আমার বন্ধু তীর্থঙ্কর তাঁদের ক্লাবের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়ার সময় জিজ্ঞেশ করেছিলেন, এই কবিতার পেছনে যে প্রছন্ন রবীন্দ্রবিদ্বেষ – তাঁর কারণটা কী? প্রেমেন্দ্র মিত্র তখন দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। উত্তরে বলেছিলেন, ওটা এক ধরনের যৌবনের উন্মাদনা। যখন যুবক ছিলেন, তখন চোখে দেখতে পেতেন, তাও তাঁকে দেখেও দেখেননি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে চোখে দেখতে পান না, পড়তে পারেন না – তবুও তাঁর অস্তিত্ব আর অনুভূতির সবকিছুই রবীন্দ্রময়।
বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়, বিশেষ করে ১৯৭২-এ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, বাঙালির জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। বিষয় ছিল, স্বাধীন বাংলাদেশের সামাজিক আর সাংস্কৃতিক পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ অপ্রাসঙ্গিক। অনেকে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ বাঙালির শ্রেণি সংগ্রামের সাথী ছিলেন না। এমনও বলা হয়েছে, তিনি বাঙালির ঐতিহ্য, কিন্তু সম্পদ নন। ঢাকা সহ বাংলাদেশের অনেক বুদ্ধিজীবী সেই বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন। ঢাকার এক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক সেই বিতর্কে নিয়মিত উস্কানি দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত এই বিতর্কে পক্ষের পাল্লাই বেশি ভারী ছিল। আশ্চর্যের বিষয় হল, সে বিতর্ক থিতিয়ে যাওয়ার পরে পরেই ওই পত্রিকার সম্পাদকের চোখের অস্ত্রোপ্রচার হয়েছিল – ঠিক তখন ওই পত্রিকার একটি সংখ্যার প্রচ্ছদ পাতায় বড় বড় করে ছাপা হয়েছিলো “অন্ধজনে দেহ আলো”। এভাবেই দুই বাঙলায় রবীন্দ্রনিন্দার সাথে সাথে হয়েছে রবীন্দ্র পঙক্তির উদ্ধারও। এগুলিকে প্যারাডক্সই বলতে হবে। সময়ের সাথে সাথে সময়ই এইসব উদ্ভট রবীন্দ্রবিচারের জবাব দিয়েছে, আর দেবেও ।
আমার মনে হয় তিনিই একমাত্র বাঙালি, যিনি তাঁর জীবদ্দশায় যত নিন্দিত হয়েছেন, তত আর কোনও বাঙালি হননি। আবার তিনিই একমাত্র বাঙালি, যিনি জীবদ্দশায় যত বন্দিত হয়েছেন, তত আর কোনও বাঙালি হননি। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ কখনও এসবের কোন উত্তর দেননি। শুধু লিখেছেন,
“নিন্দার কণ্টক মাল্য বক্ষে বিঁধিয়াছে বারে বারে
জয়মাল্য জানিয়াছি তারে।”
মন্দিরের দেবতার পুজা কোনোদিন তিনি করেননি। তিনি ধুলামন্দিরে লিখেছেন-
“নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নেই ঘরে`
তিনি আছেন যেথায়
করছে চাষা চাষ।
পাথর ভেঙ্গে
কাটছে যেথায় পথ ,
খাটছে বারোমাস।।
মানুষই তাঁর দেবতা। আজীবন তাই মানুষেরই পূজা করেছেন তিনি।
“হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে
নমি নর দেবতারে
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দনা করি তারে।”
তাঁর ভাবনায় মানুষ। তাঁর কামনায় মানুষের মঙ্গল। ভারতের জাতীয় সংগীতের প্রত্যেক অনুচ্ছেদ শুরুই করেছেন তাই মানুষকে দিয়ে – ‘জনগণমন অধিনায়ক’, ‘জনগণ মঙ্গলদায়ক’, ‘জনগণ ঐক্যবিধায়ক’, ‘জনগণ পথপরিচায়ক’, ‘জনগণ দুঃখত্রায়ক’, ‘জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা’।
তিনি ভালো বেসেছেন জগতকে, তিনি প্রণাম করেছেন মহৎকে। তিনি কামনা করেছেন মুক্তিকে, যে মুক্তি পরমপুরুষের কাছে তাঁর আত্ম নিবেদনে। আর বিশ্বাস করেছেন সেই মহামানুষের সত্যে, যিনি সদা জননং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট। সেজন্যই তিনি জাতির জনক গান্ধীজির নামের আগে মহাত্মা শব্দটি জুড়েছিলেন ।
কবিগুরুর জীবনাদর্শকে আঁকড়েই আমার বেঁচে থাকা। তিনিই আমার ঠাকুর। তিনিই আমার নিভৃত প্রাণের দেবতা।
–বিকাশ পাল, ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডন। ২৫ শে বৈশাখ , ১৪২৯।