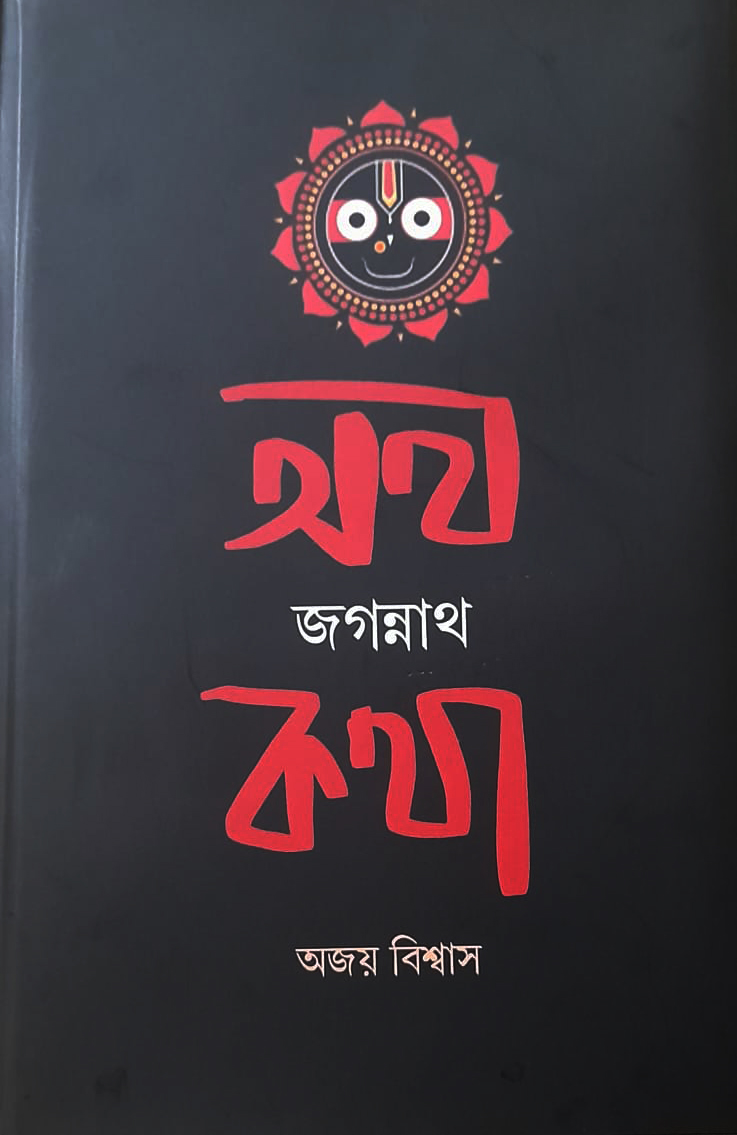শুভদীপ রায় চৌধুরী (সোমানন্দ নাথ)
দেবী জগদ্ধাত্রী, যিনি এই সমগ্র জগতকে ধারণ করে থাকেন। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে দেবীর নামের অর্থ হল, এই জগতে ভালো, মন্দ যা কিছু রয়েছে সবকিছুর সৃষ্টি এবং পালনকর্ত্রী দেবী জগদ্ধাত্রী। তাই সমগ্র বিশ্ব সংসারকে ধরে রাখা, সেই সংসারকে যথাযথ ভাবে রক্ষা করা এবং সর্বোপরি পালন করেন তিনি। তিনি নিত্যা, সনাতনী, পূর্ণব্রহ্মময়ী, তাই তাঁর শরণাগত হয় যাঁরা, তাঁদের কোনরূপ ক্ষয়, ভয় কিংবা বিনাশ করা যায় না।
বলা যায়, দেবী জগদ্ধাত্রী হলেন চৈতন্যের প্রতীক। অর্থাৎ সঠিক চেতনা লাভ হলেই সাধকের হৃদয়ে দেবী জগদ্ধাত্রীর আবির্ভাব ঘটে। যেমন, বিষ্ণু ক্রান্তার অন্তর্গত সাধকেরা বলে থাকেন যে, সাধকের হৃদয় শ্মশান না হলে সেই হৃদয়ে কখনও শ্মশানবাসিনী আসবেন না, ঠিক তেমনই। একেবারে উন্মত্ত হাতির মতন চঞ্চল মনকে যেই মুহুর্তে সাধক নিজের সঠিক চৈতন্য (সিংহের মতন শক্তি) দিয়ে দমন করতে পারবেন ঠিক তখনই তাঁর হৃদয়ের রত্নবেদীতে অধিষ্ঠান করবেন ত্রিগুণাতীতা দেবী জগদ্ধাত্রী।
এই দেবীর মূর্তিতেও বিশেষ রহস্য রয়েছে। তাঁর গাত্রবর্ণ উদিত সূর্যের ন্যায়, অর্থাৎ লাল কিংবা শিউলি ফুলের বোঁটার মতন। দেবীর অঙ্গে নাগরূপ যজ্ঞপবীত রয়েছে। দেবীর বামদিকের হাতে রয়েছে শঙ্খ ও ধনুক। আর ডানদিকের দুহাতে থাকে চক্র এবং পঞ্চবাণ। বাহনরূপী সিংহ করীন্দ্রাসুর অর্থাৎ হস্তীরূপী অসুরের পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান।
দেবীর ওপর একটি নাম করীন্দ্রাসুরনিসূদিনী, অর্থাৎ তিনি করীন্দ্রাসুর নামক এক অসুরকে সংহার করে সমগ্র জগতকে রক্ষা করেছিলেন। কাত্যায়নী তন্ত্রে দেবীর কার্তিকী শুক্লা নবমীতে আবির্ভূত হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। তবে, এ বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে দেবী জগদ্ধাত্রীর পূজা সম্পূর্ণ তান্ত্রিক পূজা, কোনো বৈদিক পূজা নয়। কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী – এই তিন তিথিতে পূজা হয়ে থাকে। তবে কোথাও কোথাও কেবলমাত্র নবমী কল্পে একসঙ্গে তিনদিনের পূজার বিধানও রয়েছে।
তবে বাংলায় দুর্গাপুজোর কিংবা কালীপূজার জনপ্রিয়তা যতটা বেশি ঠিক তেমন ভাবে জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রচলন দেখা যায় না। তবে বাংলায় প্রথম এই পূজার প্রচলন করেছিলেন নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। আবার ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায় যে, নদীয়ার শান্তিপুরে হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্রহ্মশাসনে ধ্যানে বসে চন্দ্রচূড় তর্ক চূড়ামণি জগদ্ধাত্রী পুজোর পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। বলা যায় যে, সেই স্থানেই প্রথম শুরু হয় বাংলার জগদ্ধাত্রী পুজো।
শান্তিপুরের ব্রহ্মশাসনের জগদ্ধাত্রীপুজো: নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র গিরিশচন্দ্র রায় এক সময়ে শান্তিপুরে ব্রহ্মশাসন গ্রামে ১০৮ জন ব্রাহ্মণকে বসবাসের জন্য জায়গা দেন। আর তার থেকেই জায়গার নাম হয় ব্রহ্মশাসন। এদেরই একজন চন্দ্রচূড় তর্কচূড়ামণি। তিনি সেখানেই ভাগীরথীর ধারে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে তন্ত্রসাধনা করতেন। গিরিশচন্দ্রই চন্দ্রচূড়কে অনুরোধ করেন জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রয়োজনীয় পদ্ধতি এবং মন্ত্র স্থির করতে। সেই কথা মতন ধ্যানে বসেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত চন্দ্রচূড়। আর সাধনায় বসে তিনি দেখা পান দেবীর। কথিত আছে, সেই সাধনাতেই পুজোর পদ্ধতি এবং মন্ত্রের হদিশ পান সাধক চন্দ্রচূড়। পরে সেই পদ্ধতি মেনেই তিনি ব্রহ্মশাসনে পুজো শুরু করেন। আর পরবর্তী কালে সেই পদ্ধতি অনুসরণ করেই জগদ্ধাত্রী পুজো হয়ে আসছে সর্বত্র।

আজও সেই পঞ্চমুণ্ডির আসনে ভক্তিভরে পুজো দেন ব্রহ্মশাসনের গ্রামবাসীরা। সেই আসনের সামনেই রয়েছে পুরাতন এক ভবনের ধ্বংসস্তূপ। মনে করা হয় যে, এটিই ছিল সাধক চন্দ্রচূড়ের বাড়ি। তেমন সাড়ম্বরে না হলেও আজও পুজো হয়ে আসছে চন্দ্রচূড় তর্কপঞ্চাননের সেই সাধনপীঠে যেখানে দেবী জগদ্ধাত্রী প্রথম আবির্ভূতা হয়েছিলেন। গ্রামবাসীরা সকলে মিলে সেই পুজোর আয়োজন করেন। তাই বাংলার প্রথম জগদ্ধাত্রী পুজো এই গ্রামেই শুরু হয়েছিল বলে উল্লেখ করা যেতে পারে।
কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর জগদ্ধাত্রী পুজো: তৎকালীন সময় বঙ্গের ক্ষমতায় আসীন নবাব আলিবর্দি খাঁ। তাঁর রাজত্বে মহারাজার কাছ থেকে ১২ লক্ষ টাকা নজরানা দাবি করা হয়। কৃষ্ণচন্দ্র তা দিতে অস্বীকার করলে তাঁকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয় মুর্শিদাবাদে। আর ছাড়া পেয়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যখন নদীপথে কৃষ্ণনগরে ফিরছেন ঠিক তখনই শুনতে পেলেন বিসর্জনের বাজনা। সে বছর দুর্গাপুজো করতে না পারায় অত্যন্ত দুঃখ পান তিনি।

কথিত আছে যে, সেই রাতেই রাজাকে স্বপ্নে দর্শন দেন দেবী জগদ্ধাত্রী। ঠিক দুর্গাপুজোর মতন বিধি মেনেই তাঁর পুজোর নির্দেশ দেন দেবী। সেই থেকে কৃষ্ণনগরে দুর্গাপুজোর বিকল্প হিসেবে প্রচলিত হয় জগদ্ধাত্রী পুজো। কৃষ্ণচন্দ্রের পুজোয় অনুপ্রাণিত হয়ে ফরাসিদের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী শুরু করলেন তৎকালীন ফরাসডাঙা বা অধুনা চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজো। যা পরে এক বিরাট এক উৎসবের আকার নেয়।
সাবর্ণদের জগদ্ধাত্রী পুজো: কলকাতার প্রথম দুর্গাপুজো এই পরিবারের। তবে দুর্গাপুজো ছাড়াও রায় চৌধুরী পরিবারে জগদ্ধাত্রী পুজো হয় আসছে দীর্ঘদিন ধরে। এই বাড়িতে দেবীর গায়ের রং শিউলি ফুলের বোঁটার মতন হয়, বেনারসী শাড়ি এবং প্রাচীন গয়নায় সাজানো হয় দেবীকে। দেবীর দুই পাশে দুজন ঋষি থাকেন।

শুক্ল পক্ষের নবমীর দিনই পুজো হয় বড়িশার আটচালায়। একদিনেই তিনদিনের পুজো হয়। সম্পূর্ণ আমিষ ভোগ নিবেদন করা হয় মাকে। ভোগে থাকে খিচুড়ি, সাদা ভাত, পোলাও, মাছ, তরকারি, ভাজা, চাটনি, পায়েস ইত্যাদি। আর নবমীর হোম সম্পন্ন হয় সাবর্ণদের জগদ্ধাত্রী পুজো। দশমীর দিন বরণের পর দেবী বিসর্জন হয়।
বর্ধমানের চট্টোপাধ্যায় বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো: এই বাড়ির পুজোয় গোটা গ্রাম মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। পরিবারের সদস্যরা কর্মসূত্রে কলকাতা বা দেশের নানা প্রান্তে থাকেন, তবে পুজোর সময় শিকড়ের টান উপেক্ষা করা যায় না। পুজোর ক’টা দিন সকলে একসঙ্গে আসেন পৈতৃক বাড়িতে। দেবীর প্রতিমা এখানে এক চালার এবং ত্রিনয়নী মায়ের গায়ের রং শিউলি ফুলের বোঁটার মতন। কিন্তু এছাড়াও বিশেষত্ব হল, এই প্রতিমার দু’পাশে দেখা যায় মহাভারতের রচয়িতা ব্যাসদেব এবং অপর পাশে নারদ মুনিকে।
কলকাতার দে বাড়ির পূজা: এই পরিবারের জগদ্ধাত্রী পূজা ১৮৯৭ সালে শুরু হয়, সেই ধারা আজও চলে আসছে। বংশের পূর্বপুরুষ গিরিশ চন্দ্র দে শুরু করেছিলেন এই পুজো। প্রতি বছরই কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের নবমীর দিনে ঠনঠনিয়ার দে পরিবার এই পূজা সাড়ম্বরে হয়।
ছাতু বাবু এবং লাটু বাবুর জগদ্ধাত্রী পূজা: উত্তর কলকাতার বনেদি পরিবারের অন্যতম এই বাড়ি। দুর্গাপুজোর পাশাপাশি জগদ্ধাত্রী পুজোও সাড়ম্বরে পালিত হয়। এই বাড়ির দেবী জগদ্ধাত্রীর পূজা দুশো বছরেরও পুরনো। ১৭৮০ সালে বংশের পূর্বপুরুষ রামদুলাল দে (সরকার) এই পুজো শুরু করেছিলেন।

এই বাড়িতে নবমীর দিনেই পুজো অনুষ্ঠিত হয়। দেবী জগদ্ধাত্রীকে কাঠের সিংহাসনে বসানো হয়। তবে সম্পূর্ণ তান্ত্রিক রীতি মেনেই পূজা হয়। পুজোর বৈশিষ্ট বলতে, কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। দেবী জগদ্ধাত্রীকে নিরামিষভোগ নিবেদন করা হয় এ বাড়িতে। আর দশমীর দিন কনকঞ্জলি এবং বরন হয়।
শান্তিপুরের ব্রহ্মচারী পরিবার: ১৮৯৪-৯৫ সাল নাগাদ এই বাড়িতে পুজো শুরু হয়, যা আজও চলছে। এই ব্রহ্মচারী বংশের ইতিহাস দেখলে বোঝা যায় যে, এই বংশের আদিপুরুষ চামু ব্রহ্মচারী বাস করতেন অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের নাটোরে। এই পরিবারের আদি পদবি বাগচী। সৎ-মা এবং নিজের মায়ের দ্বন্দ্বের কারণেই পৈতের সময় তিন দিনের রাত্রিবাস শেষ করার আগেই চামু দণ্ডীঘর থেকে আগেই বেরিয়ে আসেন সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য। এরপর থেকেই পরিবারের সদস্যরা বাগচীর পরিবর্তে ব্রহ্মচারী পদবি লিখতে শুরু করেন। চামু ব্রহ্মচারী অবশ্য আবার পরিবারে ফিরে এসেছিলেন, তবে তাঁদের পদবি বাগচীতে ফিরে যায়নি।
চামু ব্রহ্মচারীর উত্তরপুরুষ রামগোপাল ব্রহ্মচারী মালঞ্চ (সুভাষগ্রাম ও মোল্লিকপুরের মাঝে) থেকে বেরিয়ে শান্তিপুরে চলে যান। রামগোপালের মাতুলালয় ছিল শান্তিপুরের মৈত্র পরিবার। মৈত্র পরিবারের রজনীকান্ত মৈত্রের সঙ্গে রামগোপাল ব্রহ্মচারী ব্যাবসার কারণে সংযোগ স্থাপন করেন এবং শান্তিপুরে চলে আসেন। তিনি শান্তিপুরে নিজের বসত বাড়ি এবং আটচালা নির্মাণ করেন। নির্মাণের পরই দেবীর স্বপ্নাদেশ পান যে – কালীপুজোর পরেই আয়োজন করতে হবে জগদ্ধাত্রীপুজোর।
ব্রহ্মচারী বংশে জগদ্ধাত্রীর রঙ উদিত সূর্যের মতো লাল। এই পরিবারে একদিনেই পুজো হয় অর্থাৎ নবমী তিথিতে ত্রিকালীন পূজা। দেবীর চালচিত্রে রয়েছে হস্তশিল্পের ছোঁয়া। দেবী সিংহবাহিনী এবং রাজসিংহরূপ লক্ষ করা যায়। জগদ্ধাত্রীকে স্বর্ণালংকারে সাজানো হয়। এই পরিবারে দেবী স্বয়ং বৈষ্ণবী হলেও তাঁর পুজো হয় তন্ত্রমতে। দেবীকে সম্পূর্ণ নিরামিষ ভোগ নিবেদন করা হয়। একমাত্র শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত বাড়ির মহিলারাই ভোগ রান্না করতে পারেন।
হাওড়ার ভট্টাচার্য বাড়ি: ১৭৬৫ সালের কার্তিক মাসের শুক্লানবমীতে জগদ্ধাত্রীর আরাধনা শুরু হয় আন্দুলের ভট্টাচার্য বংশীয় গোপীমোহন ভট্টাচার্যের হাত ধরে বর্তমান হাওড়া শহরের মল্লিকফটকের বাড়িতে। গোপীমোহন (বংশের পূর্বপুরুষ) সেই বছরেই তাঁর বংশের প্রাচীন কূলদেবী শ্রীশ্রীশঙ্করীদুর্গা (কালীযন্ত্রের আধারে) এবং পারিবারিক দুর্গাপূজা নিয়ে আসেন তাঁদের আন্দুলের বসতবাটী থেকে।
গোপীমোহন দুর্গাপুজোর দায়িত্ব নিয়ে হাওড়ার মল্লিকফটকে তাঁদের বাড়িতে আসেন এবং ঠাকুরদালান নির্মাণ করে পারিবারিক দুর্গাপূজা চালিয়ে যান। শাস্ত্রমতে, দুর্গাপূজার পর আবারও শক্তিপূজা করা দরকার। কিন্তু কালীসাধক হয়েও গোপীমোহন কালীপূজা করলেন না কারণ তাঁদের বংশীয় প্রতিষ্ঠিত শঙ্করীকালী ইতিমধ্যেই অবস্থান করছেন আন্দুলে তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরে, (যা বর্তমানে আন্দুলে দেবী সিদ্ধেশ্বরী শঙ্করীকালী মন্দির হিসাবে বিখ্যাত)। তাই কালীপূজার পরিবর্তে গোপীমোহন পিতার আদেশ মেনে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পুজো শুরু করেন। সেই পূজাই তাঁর পুত্র রামনারায়ণ হতে সাত পুরুষ ধরে মল্লিকফটকের বাড়িতে হয়ে আসছে।
এই বাড়িতে শুক্লানবমীতেই সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমীর পূজা হয়। মহাস্নানে ডাবের জল আবশ্যিক কারণ সেটি দক্ষিণাচারী তান্ত্রিক আচার। দেবীর বাঁ হাতে শঙ্খের জায়গায় থাকে খড়্গ। আগে পাঁঠাবলি হলেও ১৯৮৪ থেকে প্রাচীন হাঁড়িকাঠে চালকুমড়ো, বাতাবিলেবু এবং আখবলি হয়। নবমীপূজায় বলিদান এবং অষ্টমীতে ২৮টি দীপ দান হয়। মাকে মাছভোগ দেওয়া হয়ে থাকে এবং ‘নবান্ন’ নৈবেদ্য নিবেদিত হয়। ‘নবান্ন’য় জোড়া কড়াইশুঁটি, চাল আর নতুন নলেনগুড় হল আবশ্যিক।
কলকাতার পাল বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো: ১৩০৭ বঙ্গাব্দে (১৯০০ খ্রিস্টাব্দে) এই পুজো শুরু করেছিলেন পরিবারের পূর্বপুরুষ বটকৃষ্ণ পাল। পাল পরিবারের আদি নিবাস হাওড়ার শিবপুরে। মাত্র ১২ বছর বয়সে কলকাতায় মামার বাড়িতে চলে আসেন তিনি। আর একটু বড়ো হয়েই শুরু করেন ব্যবসা। কালক্রমে সেই ব্যবসা বৃহৎ আকার ধারণ করে। প্রখ্যাত ওষুধ ব্যবসায়ী ও প্রস্তুতকারক হিসাবে তাঁর নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ‘বটকৃষ্ণ পাল অ্যান্ড কোং’।
বটকৃষ্ণ পাল ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে উত্তর কলকাতার ৭৭ বেনিয়াটোলা স্ট্রিটে জমি কিনে বসতবাড়ি নির্মাণ করেন, এবং সেই বাড়িতে এক সুন্দর কারুকার্যখচিত ঠাকুরদালান তৈরি করেন। এই ঠাকুরদালানেই ১৩০৭ বঙ্গাব্দে মহাসমারোহে জগদ্ধাত্রীর পুজো শুরু হয়।
পাল বাড়ির দেবী জগদ্ধাত্রীর বিশেষত্ব হল, বাহন সিংহের পিঠে মা দু’ পা মুড়ে বাবু হয়ে বসে আছেন। মায়ের সঙ্গে রয়েছেন তাঁর চার সখী। মাকে স্বর্ণালংকারে ভূষিত করা হয়। দিনে তিন বার পুজো ছাড়াও হয় সন্ধিপুজো। তাতে আধ মণ চালের নৈবেদ্য, গোটা ফল, ১০৮ পদ্ম ও প্রদীপ নিবেদন করা হয়। দেবীর নিরঞ্জনের সময় লরিতে চৌকির ওপর চালচিত্র সমেত সখী-সহ মাকে অধিষ্ঠিত করা হয়। বিসর্জনের সময় শোভাযাত্রা আরও এক ঐতিহ্য।
(লেখক আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক এবং আচার্য, বগলামুখী মাতৃ মিশন)