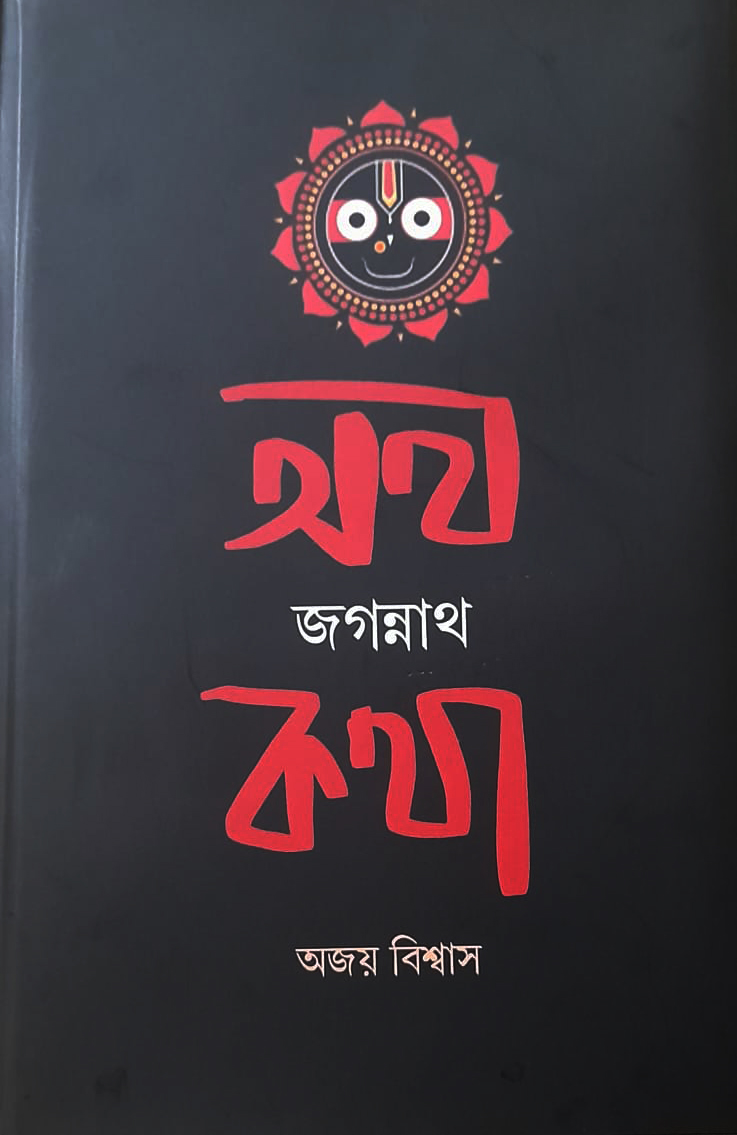বোধহয় একেই বলে ঠাকুরের ইচ্ছে। এমনই তাঁর মাহাত্ম্য। আজ যে বিস্তৃত ভূখণ্ডে বিশ্ববিখ্যাত বেলুড় মঠ, তারই অন্তত একাংশে একসময় চরণচিহ্ন এঁকে দিয়ে গিয়েছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং।
স্বামী বিবেকানন্দ মঠের জন্য ওই জমি কিনেছিলেন বিহারী ভদ্রলোক বাবু ভাগবৎনারায়ণ সিংয়ের কাছ থেকে। ছোট দুটি বাড়িসমেত ২২ বিঘা। ১৮৯৮ সালের ৪ মার্চ। তবে স্বামীজির জানা ছিল না যে, তারও আগে ওই জমিতেই ছিল ঠাকুরের গৃহী ভক্ত ‘কাপ্তেন’ বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের কাঠগোলা। সেখানেই একদা পদধূলি দিয়েছিলেন ঠাকুর। আমরা জানি, ঠাকুর মর্তলীলা সংরবণ করেন ১৮৮৬ সালের ১৬ আগস্ট। অর্থাৎ বেলুড়ে ওই জমি কেনার অনেক আগেই ঠাকুর সেখানে গিয়েছিলেন। যেন স্থায়ী মঠ স্থাপনের উদ্দেশ্যেই সেখানে ‘কুটোবাঁধা’ হয়ে গিয়েছিল। স্থায়ী মঠের জন্য অন্যত্র জমি সংগ্রহের সকল চেষ্টাই শেষাবধি ব্যর্থ হয়েছিল। এই ঘটনাকে দৈবনির্ধারিত ছাড়া কীইবা বলা যায়।
বিশ্বনাথ উপাধ্যায় ছিলেন নেপালের রাজার ভারতে নিযুক্ত উকিল। রাজপ্রতিনিধিরূপেই তিনি কলকাতায় বাস করতেন। বেলুড়ে নেপালরাজের একটি কাঠগোলা ছিল। প্রথম দিকে বিশ্বনাথ উপাধ্যায় ওই কাঠগোলাতেই কর্মচারী নিযুক্ত হন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভমাত্রই তিনি ঠাকুরের পরম ভক্ত হয়ে ওঠেন। ঠাকুর তাঁকে আদর করে ‘কাপ্তেন’ ডাকতেন। কাপ্তেনের অনুরোধেই ঠাকুর বেলুড়ের ওই কাঠগোলা ঘুরতে যান।
ওই স্থান মাহাত্ম্য সম্পর্কে স্বামী গম্ভীরানন্দ এক স্থানে সারদা দেবীর মুখে বলেছিলেন,
‘‘আমি কিন্তু বরাবরই দেখতুম, ঠাকুর যেন গঙ্গার ওপরে এই জায়গাটিতে—যেখানে এখন (বেলুড়) মঠ, কলাবাগান-টাগান—তার মধ্যে ঘর, সেখানে বাস করছেন।’’
জমিটি সংগ্রহের পর শ্রীমা আরও বলেছিলেন, জমিটা ঠাকুরের ইচ্ছাতেই হল। মঠের জন্য জমিটা তিনিই নির্বাচন করে গিয়েছিলেন!
বেলুড়ে জমি তো কেনা হল। কিন্তু তা অসমতল। অতএব সেখানে মঠ নির্মাণ করতে একটু সময় লাগবে, তার তদারকিও দরকার। অতএব বেলুড়েই কাছাকাছি নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ি ভাড়া নেওয়া হল। মঠ অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হল সেখানেই। বারাণসীর সমতুল গঙ্গার পশ্চিম তীরের এই বাড়িতেই শ্রীমা বসবাস করার সময় ছোট ছাদে পঞ্চতপা ব্রত করেছিলেন। সদ্য-কেনা কাপ্তেনের কাঠগোলার মঠভূমিতে ঠাকুরকে স্বামীজি প্রতিষ্ঠা করেন এই বাড়ি থেকেই। ১৮৯৮ সালের ৯ ডিসেম্বর স্বামীজি নতুন মঠের জমিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ‘আত্মারাম’কে পুজো করে পায়েস নিবেদন করেন। আর সকাতরে প্রার্থনা করেন, ঠাকুর তুমি ‘বহুজনহিতায়’ এখানে স্থির হয়ে থেকো।
বেলুড় মঠে দাঁড়িয়ে গুরুভাইদের বিবেকানন্দ সেদিনই বলেছিলেন,
“কাশীপুরে ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, ‘তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব ও থাকব। তা গাছতলায় কি, আর কুটিরই কি।’ সেজন্যই আমি স্বয়ং তাঁকে কাঁধে করে নতুন মঠভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয় জানবি, বহুকাল পর্যন্ত ‘বহুজনহিতায়’ ঠাকুর ওই স্থানে স্থির হয়ে থাকবেন।
প্রত্যেক ভক্ত ঠাকুরকে আপন বুদ্ধির রঙে রাঙিয়ে এক-এক জনে এক-এক রকম দেখে ও বোঝে। তিনি যেন মহাসূর্য, আর আমরা যেন প্রত্যেকে এক-এক রকম রঙিন কাচ চোখে দিয়ে সেই একই সূর্যকে নানা রং-বিশিষ্ট বলে দেখছি। এটি ঠিক সেই ভাবের কেন্দ্রস্থান হবে। এখান থেকে যে মহাসমন্বয়ের উদ্ভিন্ন ছটা বেরবে তাতে জগৎ প্লাবিত হয়ে যাবে। ঠাকুরের ইচ্ছেয় আজ তাঁর ধর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা হল। বারো বছরের চিন্তা আমার মাথা থেকে নামল। আমার মনে এখন কী হচ্ছে জানিস? এই মঠ হবে বিদ্যা ও সাধনার কেন্দ্রস্থান। … সময়ে সব হবে। আমি তো পত্তন-মাত্র করে দিচ্ছি। এর পর আরও কত কী হবে !”
জীবনের উপান্তে এসে স্বামীজি বলেছিলেন,
“আমি যে নিষ্কর্মা সাধু হয়ে থাকিনি, সে বিষয়ে অন্তর থেকে আমি নিঃসন্দেহ। প্রাণ ঢেলে খেটেছি। আমার কাজের মধ্যে সত্যের বীজ যদি কিছু থাকে, কালে তা অঙ্কুরিত হবেই।”
শ্রীশ্রীমাও এই মঠভূমি দেখতে এসেছিলেন। তাই পরে তিনি বলেছিলেন, অত্যন্ত শান্ত জায়গা বেলুড়ে তিনি খুব ভালো ছিলেন। তাঁর ধ্যান লেগেই থাকত। তাই ওখানে একটি ‘স্থান’ করতে নরেনের ইচ্ছে হয়েছিল।
শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দেশিত পথে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ গঠন করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৮৬ সালে। অর্থাৎ ঠাকুর যে-বছর দেহসংবরণ করলেন সে-বছরই। বরাহনগরের এক জীর্ণ বাড়িতে। যা ‘বরাহনগর মঠ’ নামে রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যে সুপরিচিত। সুদীর্ঘ ৩৪ বছর এই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে লালিত ও পালিত করেছেন সঙ্ঘজননী সারদা দেবী। সেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বাস্তব রূপ দিলেন স্বামী বিবেকানন্দ বাগবাজারে বলরাম মন্দিরে ১৮৯৭ সালের ১ মে। নাম হল রামকৃষ্ণ মিশন। আর বরাহনগর মঠ রূপান্তরিত হল ‘রামকৃষ্ণ মঠ’-এ। এই বরানগরে থাকতেই বিবেকানন্দের মন ঠিক করে নিয়েছিল স্থায়ী মঠ ঠিক কোথায় হবে। বরাহনগর খেয়াঘাটে দাঁড়িয়ে তিনি একদিন গুরুভাইদের বলেছিলেন, আমার কেন যেন মনে হচ্ছে গঙ্গার ওপারে কাছেপিঠেই আমাদের স্থায়ী মঠটি হতে চলেছে।
বেলুড় মঠের জমি কেনার পর স্বামীজি সওয়া চার বছর জীবিত ছিলেন। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই তিনি মঠ প্রতিষ্ঠার মূল কাজগুলি সাঙ্গ করে গিয়েছিলেন। মিশন তৈরির পর তার কলকাতা কেন্দ্রের ভার দেওয়া হয়েছিল স্বামী ব্রহ্মানন্দকে। অন্যদিকে, ১৮৯৮ সালে বেলুড়ে নতুন মঠ নির্মাণের কাজ শুরু হলে তার দায়-দায়িত্বও ব্রহ্মানন্দের ওপর ন্যস্ত হল। পরের বছর আলমবাজার থেকে বেলুড়ে নতুন বাটিতে মঠ উঠে আসার পর বেলুড় মঠ পরিচালনার ভারও তাঁকে নিতে হল। অবশেষে ১৯০০ সালের আগস্টে দলিল তৈরি করে মঠের যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি স্বামীজি গুরুভাইদের হাতে তুলে দিলেন। আর ১৯০১ সালের গোড়ার দিকে মঠ ও মিশনের সাধারণ সভাপতির আসন ত্যাগ করলেন স্বামীজি। অতঃপর স্বামী বিবেকানন্দের স্থলাভিষিক্ত হলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। ঠাকুর বলেছিলেন,
‘রাখাল একটা সাম্রাজ্য চালাতে পারে।’
বিবেকানন্দ এবং তাঁর গুরুভাইরা রাখাল মহারাজের উপর ঠাকুরের এই অগাধ আস্থার কথা ভোলেননি। মঠ কী আকার নেবে স্বামীজি তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন অপর গুরুভ্রাতা স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে, পূর্বাশ্রমে যিনি ছিলেন একজন দক্ষ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। মন্দিরের প্রতীক স্বামীজি তৈরি করার পর মন্দিরের নকশা স্বামীজির তত্ত্বাবধানে তৈরি করেছিলেন বিজ্ঞানানন্দজি।
স্বামীজি শুধু এক বাগ্মী হিন্দু সন্ন্যাসী ছিলেন না, একই সঙ্গে ছিল তাঁর শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান সমাজ রাজনীতি দর্শন প্রভৃতি সম্পর্কে অত্যন্ত আধুনিক চিন্তা চেতনা। ভারত এককালে ছিল শিল্পের দেশ। কিন্তু স্বামীজির জীবদ্দশায় ভারতের শিল্পচেতনা লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছিল। দেশের এই হতশ্রীদশা তাঁকে নিরন্তর আহত করত। তাই সঙ্কল্প করেছিলেন, বেলুড় মঠের ভেতর দিয়েই ভারতীয় শিল্পচেতনা বিকাশের পুনর্নবীকরণ করবেন। সাহেবদের শিল্পভাবনার হুবহু নকল করে বেলুড় মঠ নির্মিত হবে না—যা তৎকালীন ভারতের এক ব্যাধি হয়ে উঠেছিল। বেলুড় মঠের প্রতীক ও নকশায় আমরা স্বামীজির ওই দেশজ এবং মিশ্র শিল্পভাবনার সমন্বয়ের প্রতিফলনই প্রত্যক্ষ করি। বেলুড়ে বর্তমান মন্দিরটির উদ্বোধন হয় ১৯৩৮ সালের ১৪ জানুয়ারি পৌষ সংক্রান্তির দিন। মঠের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ নতুন মন্দিরে ঠাকুরকে স্থাপন করেন। মঠের পুরনো মন্দির থেকে বুকে করে আত্মারামকে নিয়ে এসে নবনির্মিত মন্দিরে ঠাকুরের মূর্তির সামনে রেখে প্রার্থনা করেন। সেইসময় তিনি প্রত্যক্ষ করেন স্বামীজিসহ তাঁর অন্য গুরুভাইরা সূক্ষ্ম শরীরে উদ্বোধন দেখতে মন্দিরে উপস্থিত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, ১৯২৯ সালের ১৩ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ মন্দিরের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করেন। তবে, পরে মন্দির গড়ে তুলতে গিয়ে তার স্থান সামান্য পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়। তাই ১৯৩৫ অব্দের গুরুপূর্ণিমাতে সেই তাম্রফলকটি সরিয়ে দ্বিতীয়বার স্থাপন করেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। পরের বছর ১০ মার্চ থেকে মন্দিরের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়। ঠিক ছিল যে ১৯৩৭ সালে জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন মন্দির প্রতিষ্ঠার কাজ শেষ হবে। কিন্তু গর্ভমন্দিরের কাজ শেষ করতে কিছুটা দেরি হওয়ায় তিনি দুঃখ পেয়ে বলেছিলেন,
‘তোমরা বাপু বড় দেরি কর! স্বামীজি মন্দিরের প্ল্যান করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সময়ে মন্দির হয়নি। রাজা মহারাজা চেষ্টা করেও পারেননি। মহাপুরুষ মহারাজ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেও পারলেন না। সবাই একে একে চলে গেলেন। তাই বলছি, যত শীঘ্র পার তোমরা কাজ শেষ করে নাও, আর দেরি কোরো না।’
বিজ্ঞানানন্দজির কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করলেন সকলে। তাই নাটমন্দিরের কাজ সমাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা না-করেই ১৯৩৮-এর ১৪ জানুয়ারি গর্ভমন্দিরে ঠাকুরের মর্মরবিগ্রহ স্থাপনসহ মন্দির প্রতিষ্ঠার কাজ সমাপনের সঙ্কল্প নেওয়া হল। সেদিন নতুন মন্দিরে আত্মারামের কৌটা স্থাপনের পর স্বামী বিজ্ঞানানন্দ নিজ কক্ষে ফিরে গিয়ে স্বামীজির উদ্দেশে বলেছিলেন,
‘স্বামীজি, আপনি ওপর থেকে দেখবেন বলেছিলেন। আজ দেখুন, আপনারই প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর নতুন মন্দিরে বসেছেন।’
বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ আরও ‘স্পষ্ট’ দেখতে পেয়েছিলেন যে, স্বামীজি, রাখাল মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাজ প্রমুখ সকলেই দাঁড়িয়ে আছেন। এর কিছুক্ষণ পরে তিনি স্বস্তির ও তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন এই বলে যে,
‘এবার আমার কাজ শেষ হল। স্বামীজি আমার ওপর যে কাজের ভার দিয়েছিলেন, সে ভার আজ আমার মাথা থেকে নেমে গেল।’
নাটমন্দির সমেত সমগ্র মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ২৩৫ ফুট আর প্রস্থে ১৪০ ফুট। দ্বিতল গর্ভমন্দিরটি ১১২ ফুট উঁচু। ঠাকুরের দেহাবশেষ যে তাম্রপাত্রে রক্ষিত ছিল সেই আত্মারামের কৌটা এবং ঠাকুরের ধ্যানমূর্তি নতুন মন্দিরের গর্ভগৃহে স্থাপন করা হয়। উচ্চ যোগাবস্থায় স্থিত ঠাকুরের ধ্যানস্থ মূর্তিটির ভাস্কর ছিলেন গোপেশ্বর পাল। ঠাকুরের মূর্তিটি যাতে দূর থেকেও সকলে ভালোভাবে দেখতে পান, সেইরকমভাবেই সেটি ডম্বরু আকৃতির বেদিতে উঁচু করে বসানো হয়েছে। ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুরে যুগীদের শিবমন্দিরের আদলে বেদিটি তৈরি। বেদির সামনে ব্রাহ্মীহংসটি উৎকীর্ণ করা হয়েছিল ভারত বিখ্যার শিল্পী নন্দলাল বসুর নির্দেশমতো। নাটমন্দিরের সামনে প্রধান প্রবেশপথের ওপরের দিকে মঠ ও মিশনের প্রতীক স্থাপন করা হয়েছে।
মন্দিরের পেছন দিকে নীচের তলাটি ব্যবহার করা হয় নিত্যপূজার ভাঁড়ার হিসেবে। পূজার সরঞ্জামগুলি রাখা হয় মন্দিরের ভেতরের দেওয়ালে কয়েকটি কুলুঙ্গিতে। এর মধ্যে একটিতে রাখা হয় বাণলিঙ্গ শিব এবং একটিতে থাকে শ্রীমায়ের পবিত্র পদধূলি। আর দোতলার ঘরটি ঠাকুরের শয়নকক্ষ নামে চিহ্নিত হয়েছে। এখানেই সারা বছর সযত্নে রক্ষিত থাকেন আত্মারাম, যা বছরে তিনবার মন্দিরে নামিয়ে এনে মহাস্নান করানো হয়—স্নানযাত্রা, ঠাকুরের জন্মতিথি ও দুর্গাপূজার মহাষ্টমীর দিন। ঠাকুরের ব্যবহৃত স্মারক দ্রব্যগুলি সযত্নে রক্ষিত একতলার ঘরে।
এখানে গর্ভমন্দির ও নাটমন্দির একসঙ্গে যুক্ত, যা সাধারণভাবে হিন্দুমন্দিরে দেখা যায় না, বরং খ্রিস্টীয় রীতিসম্মত। মন্দিরের গম্বুজগুলিতে মসজিদের ছাপ পাওয়া যায়। ছত্রীগুলির ধারে কামারপুকুরে ঠাকুরের বাসগৃহের আদল স্পষ্ট হয়। গম্বুজের স্থাপত্যরীতির সঙ্গে ওড়িশা মন্দিরস্থাপত্যের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। নাটমন্দিরের বাঁকানো ছাদ ও বারান্দায় বৌদ্ধ গুহাশিল্পের কথা মনে করিয়ে দেয়। মন্দিরে প্রবেশপথের গোপুরমটি তৈরি করা হয়েছে অজন্তা ও ইলোরার রীতির আদলে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন ‘যত মত তত পথ’ নামক সবচেয়ে উদার ধর্মমতটির প্রবক্তা। বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরটিতে সেটিই বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।
আমরা জানি, আমেরিকা, ব্রিটেনসহ সমগ্র পাশ্চাত্যে স্বামীজির কী বিরাট প্রভাব ছিল। রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠার সময়েও তাঁদের অনেকে কুণ্ঠাহীনভাবে স্বামীজির পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দু’জন হলেন ইংরেজ কন্যা কুমারী হেনরিয়েটা এফ মিলার এবং আমেরিকান শিষ্যা ওল বুল। বেলুড় মঠের জমি কেনার সময় তাঁরা অকৃপণ হাতে অর্থ সাহায্য দিয়েছিলেন। আর ছিল দেশবাসীরও প্রসারিত হাত। এঁদের সকলের সহযোগিতা ছাড়া আজ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ এই উচ্চতার পৌছঁতে পারত কি না সংশয় রয়ে যায়। অনটনের কারণে স্বয়ং স্বামীজিরও এক সময় অভরসা ধরে গিয়েছিল। কিন্তু শশী মহারাজকে (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) টলানো যেত না। কিছু অর্থের সংস্থান করার জন্য তিনি সাময়িকভাবে স্থানীয় এক স্কুলে মাস্টারিও করেছিলেন। মঠকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন সুরেশ মিত্র ও বলরাম বসু। তাঁদের মৃত্যুর পরই অনটনটা যেন বেশি টের পাওয়া গিয়েছিল। বিদেশে বক্তৃতা করেও টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করতেন স্বামীজি। গুরুভাইদেরও কেউ কেউ তীর্থে তীর্থে বেরিয়ে পড়েছিলেন। রসিদ কেটে চাঁদা আদায়ও চলত। খেতড়ির রাজাও কিছু টাকা দিয়েছিলেন। অর্থ সাহায্য এসেছিল মিস সাউটার, মিস জোসেফিন, মিস্টার স্টার্ডিসহ কিছু পশ্চিমি বন্ধু বা ভক্তদের কাছ থেকে। তবে যেখান থেকে যত টাকাই আসুক না কেন, স্বামীজির নির্দেশ ছিল, নির্দিষ্ট খাতের টাকা অন্যখাতে ব্যয় করা চলবে না।
এইভাবে স্বামীজির নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ যখন এগিয়ে চলেছে, তখনই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! ১৯০২ সালের ৪ জুলাই স্বামীজি দেহত্যাগ করলেন। এই ঘোর দুঃসময়েও টলমল তরী যে যথার্থই কূলে ভিড়তে পেরেছিল তার জন্য সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দিতে হবে সঙ্ঘজননী শ্রীমা এবং তাঁর দুই ভক্ত স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দকে।
আরও একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন গোড়াতেই ঘোষণা করেছিল যে, তারা রাজনীতির সংস্রব মুক্ত। তা সত্ত্বেও পরাধীন ভারতের ব্রিটিশ সরকার এই মঠ ও মিশনকে যথেষ্ট সন্দেহের চোখে দেখত। ভাবত, এটা সন্ত্রাসবাদীদের আখড়া। তাদের সম্পর্কে বিরাট এক বিরূপ রিপোর্টও তৈরি করেছিল পুলিস।
প্রখ্যাত বিবেকানন্দ-গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু মন্তব্য করেছেন,
‘স্বামীজির কল্পনায় এই মন্দির ভারতবর্ষে শিল্পের নবজাগরণের গর্ভগৃহ।’
কাশীপুরে একটি ভাড়া-করা বাড়িকে লক্ষ্য করে স্বামী বিবেকানন্দ ‘আমাদের প্রথম মঠ’ বলেছিলেন। যে বাড়িতে ঠাকুর তাঁর মর্তলীলা সংবরণ করেছিলেন। রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন এখানে ঠাকুরকে কেন্দ্র করেই দানা বেঁধেছিল। পরে বরাহনগর, আলমবাজার হয়ে তা বেলুড়ে পৌঁছায়। এই পর্বে আন্দোলনটি আবর্তিত হয়েছে বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরুভ্রাতাদের মাধ্যমে। ঠাকুরের গৃহীভক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্রের আগ্রহে ও পরামর্শে বরাহনগর মঠ স্থাপিত হয়েছিল। অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর তপোবন যদি হয় রামকৃষ্ণ ভাবধারার গোমুখ, তবে বেলুড় হল তার গঙ্গোত্রী। শতাধিক বর্ষকালব্যাপী প্রবাহিত সেই অমৃতধারা বেলুড় মঠের মধ্য দিয়েই মানবমুক্তির পথে এগিয়ে চলেছে।
অকালমৃত্যু ও অকালবার্ধক্যের এই দেশে স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কোন শক্তির বলে এমন কালজয়ী হল, তা একালের ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞদের কাছে রীতিমতো কৌতূহলের বিষয়। অন্যের অর্থ গ্রহণ ও পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রেখে তা সুষ্ঠুভাবে ব্যয়। এমপাওয়ারমেন্ট বা ক্ষমতাপ্রদানের মাধ্যমে সংগঠনের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগ্রত রাখা। সংগঠনটি আরও দেখিয়ে চলেছে প্যাশন বা আবেগ, মোটিভেশন বা উৎসাহ, কঠোর পরিশ্রম, নির্মোহ হয়ে সবার জন্য উন্নয়ন চিন্তা কতখানি ফলপ্রসূ। বিবেকানন্দের হাতে-গড়া এই সংগঠন দেখিয়ে চলেছে—নিজের মোক্ষ, জগতের মঙ্গল এবং একই সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মের শৃঙ্খলা—তিনটি আপাত বিপরীতধর্মী শক্তির সমন্বয় কীভাবে করা সম্ভব। সব মিলিয়ে সাহিত্যিক শংকরের মনে হয়েছে যে, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন হল এক ম্যানেজমেন্ট-বিস্ময়।
ভারত এবং বহির্ভারত মিলিয়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মোট শাখা আজ ১৮০টি! বেলুড় যার প্রাণকেন্দ্র। ১৯৯৩ সালের ৮ অক্টোবর ইউনেস্কো বিল্ডিংয়ে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও বিদ্বজ্জনদের এক সমাবেশ হয়। সেদিন ইউনেস্কোর ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ ফ্রেডেরিকো মেয়রের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য,
‘১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দ যে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করেছিলেন তার সংবিধানের সঙ্গে ১৯৪৫ সালে তৈরি ইউনেস্কোর সাদৃশ্য দেখে আমি খুবই বিস্মিত হই। উন্নতির লক্ষ্যে উভয়েরই যে কর্মপ্রচেষ্টা, তার কেন্দ্রে রয়েছে মানুষ।’
স্বামী সত্যানন্দ মহারাজ
(ফেসবুক থেকে নেওয়া)