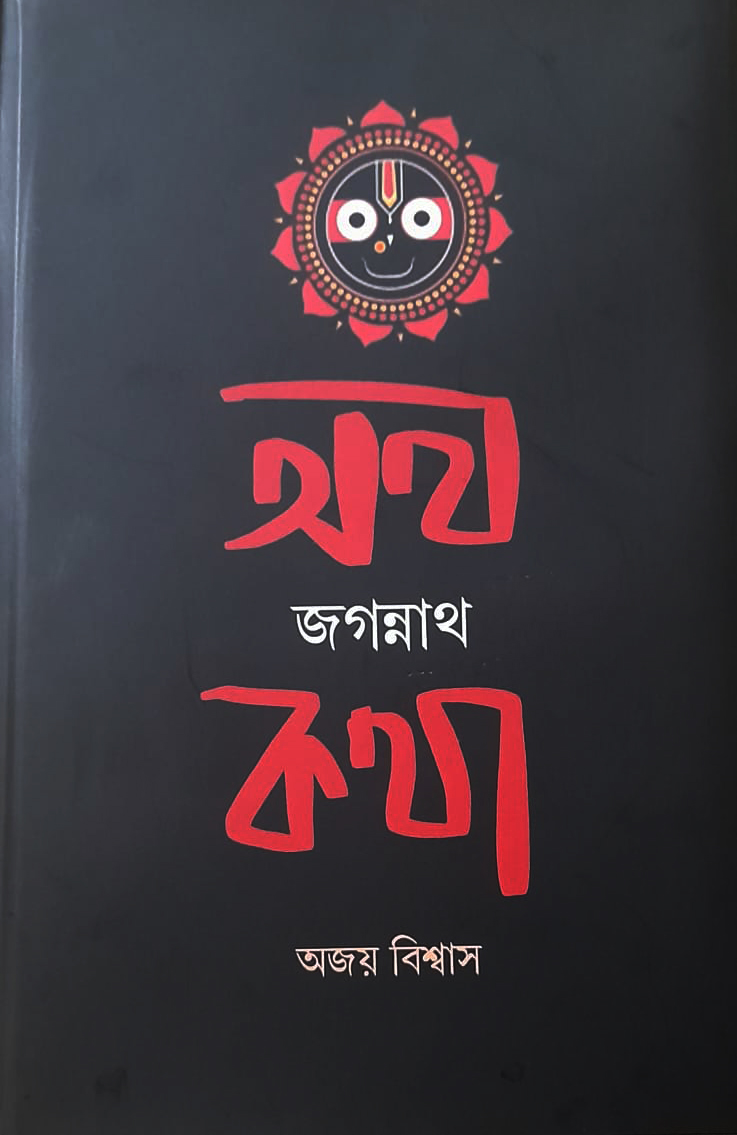ডঃ বিকাশ পাল, লন্ডন
“খ্যাতি নিন্দা পার হয়ে জীবনের এসেছি প্রদোষে,
বিদায়ের ঘাটে আছি ব’সে।
আপনার দেহটারে অসংশয়ে করেছি বিশ্বাস,
জরার সুযোগ পেয়ে নিজেরে সে করে পরিহাস”, – আরোগ্য
১৯৪১ সালের শুরুর দিক। কয়েক মাস যাবৎ কবির শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। ভাদ্র মাসে হাওয়া বদল করার জন্য কালিম্পঙে ছিলেন পুত্রবধু প্রতিমাদেবীর তত্ত্বাবধানে। সেখানেও সুবিধা হল না, জ্বর মাঝে মধ্যে লেগেই থাকত, তাই প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পরামর্শে জোড়াসাঁকোতে কবিকে আনা হল দার্জিলিং থেকে। বেশ কিছু দিন অনেকের আদর যত্নে কবি অনেকটা সেরে উঠলেন। শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। ফিরেই পৌষমেলা, মাঘোৎসব সহ বিশ্বভারতীর নানান কর্মকান্ডে ডুবে গেলেন । জোড়াসাঁকোতে কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়ার পর একটু আরাম বোধ করলেও শান্তিনিকেতনে ফেরার পর শরীর আবার বেজুত হতে লাগল।
চিকিৎসকেরা কবিকে পরীক্ষা করে বুঝলেন কবির প্রস্টেট গ্রন্থি স্ফীত হয়েছে। তাই শরীরে এত জ্বালা যন্ত্রণা। অস্ত্র প্রচারের প্রয়োজন। কবির তাতে ঘোর আপত্তি। তিনি আয়ুর্বেদী কবিরাজিতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। তাঁর ৬ ফুট ২ ইঞ্চি লম্বা সুঠাম দিব্যকান্তি চেহারা। শিলাইদহে তিনি কতবার সাঁতরে পদ্মা পার হয়েছেন, কৈশোরে কুস্তি লড়েছেন, যৌবনে টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়েছেন। ছোট থেকেই এক নীরোগ অটুট চেহারার অধিকারী তিনি। তাঁকে ঈশ্বর একেবারে অন্য ধাতুতে গড়েছেন। সেই শরীরের কাটাছেঁড়া হোক, কবি মোটেই তা চান না। অথচ শরীর জুতসই না থাকায় কাজ করতে অসুবিধা। তবে লেখালেখি বন্ধ হল না। উদয়নের বসার ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে দিনের বেলা গাছের পাতা ঝরার দৃশ্য আর রাতের তারায় ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। স্মৃতিমেদুর হয়ে দুঃখ সুখে ভরা জগৎ আর জীবনের দিকে ফিরে তাকান। আপন মনে বলে চলেন:
“ঝরা পাতা গো,
আমি তোমারি দলে”
দু সপ্তাহের মধ্যেই লিখে ফেললেন আরোগ্য কাব্যগ্রন্থের সব কবিতা। তিনি মহাকালদর্শী, মানুষের সভ্যতায় মানুষই তাঁর কাছে শেষ কথা, রাজা নন, সম্রাট নন, আর শাসকও নন। তাই আরোগ্যের সেই বহুশ্রুত কবিতায় লিখলেন (ফেব্রুয়ারি ১৯৪১)
‘কত কাল দলে দলে গেছে কত লোকে,
সুদীর্ঘ অতীতে
জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে।
এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল,
এসেছে মোগল –
উড়ায়েছে ধুলিজাল
উড়িয়াছে বিজয়পতাকা
শূন্যপথে চাই
আজ তার কোন চিহ্ন নাই।
মাটির পৃথিবীর দিকে তিনি তাকিয়ে দেখতে পান মানুষের মহাকলরব। সেখানে তাঁদের গুরু গুরু গর্জন গুন গুন স্বরে দিনরাত্রি গাঁথা পড়ে দিনযাত্রা মুখরিত হয়ে চলেছে; যুগ থেকে যুগান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে। তাঁদের দুঃখ আর সুখেই পৃথিবীতে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি মন্দ্রিত হয় – শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষের পরেও তাঁরাই কাজ করে যায়।
কয়েক মাস পরেই নতুন বাংলা বছর এল। ১লা বৈশাখ কবি লিখলেন ‘সভ্যতার সংকট’-এর মত কালজয়ী প্রবন্ধ। ২৫শে বৈশাখ তাঁর ৮১ তম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে সে প্রবন্ধ পাঠ করলেন অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন। যে কবি ইউরোপীয় কবি চিন্তানায়কদের আজীবন অনুরাগী, যিনি মিল্টন, বায়রন, কীটস, শেক্সপিয়র, স্যামুয়েল জনসনের গুণমুগ্ধ আর তাঁদের সৃষ্টির মহত্বকে আজীবন প্রণাম করে এসেছেন, সেই কবি জীবনের শেষ লগ্নে এসে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধকার দিকগুলির কথা তুলে ধরলেন। সে সভ্যতায় মানুষের শক্তির আস্ফালন আছে, মুক্তির আয়োজন নেই। সেখানে লোভ বেশি, ত্যাগ কম। অবশ্য এই উপলব্ধি কবির অনেক আগেই হয়েছিল; ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরিতে এসবের উল্লেখ আছে।
শরীর ক্রমশ খারাপের দিকে। মাঝে মধ্যে হাতের আঙুলে জোর পান না। সেজন্য লিখতেও অসুবিধা। কবি বুঝতে পারছেন এ শরীর আর শক্ত হবে না। সেজন্য বিশ্রাম করে জীবনের শেষ দিনগুলি তিনি মোটেই নষ্ট হতে দেবেন না। তাই অশক্ত শরীরেই অন্যের সাহায্য নিয়ে লিখছেন। ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের অনুরোধ এল অস্ত্রোপচারের জন্য। কবির ইচ্ছে নেই। কবির বহুদিনের বন্ধু ডাক্তার নীলরতন সরকারও বললেন, অন্যদের থেকে কবির শরীর অনেক আলাদা। তিনি বহুদিন ধরে তাঁকে দেখে আসছেন – কবির শরীরটি নিখুত ভাবে বাঁধা একটি তানপুরার মত। বাইরে থেকে একটু আঘাত পেলে ভেঙে যাবে। কাটাকাটি করার দরকার নেই । বিধানবাবু দুজনকেই আশ্বস্ত করলেন সফল অস্ত্রোপচারে তিনি অন্তত আরো বছর দশেক নীরোগ শরীরে বাঁচতে পারবেন। লোকাল অ্যানাস্থেসিয়া দিয়ে হয়ে যাবে। তাঁকে কলকাতায় আনার ব্যবস্থা করা হল।
২৫ জুলাই কলকাতার উদ্দেশ্যে কবি রওনা হলেন। শান্তিনিকেতনে স্ট্রেচারের সাহায্যে কবিকে বাসে তোলা হল। সেদিন আশ্রমের ফুল পাখি মানুষ আর কবি – সকলেই বুঝে গিয়েছেন এ দেখাই শেষ দেখা। তাই বাস আশ্রমের সমস্ত রাস্তা ঘুরে বোলপুর স্টেশনে এল। আর চোখের জল ঢাকার জন্য কবির চোখে কালো চশমা। বিকেলে জোড়াসাঁকোতে এসে পৌঁছলেন। কয়েকদিনের বিশ্রামের পর অস্ত্রোপচার হবে। কবিকে দিনক্ষণ জানানো হয়নি। রানী চন্দ কবির কথা শুনে তাঁর কবিতা কাগজে লিখে রাখেন।
কবি দোতলার ঘরে পালঙ্কে শুয়ে আছেন। ঘরের পশ্চিম দিকের জানালা দিয়ে শেষ বিকেলের সূর্যের আলো কবির চোখে পড়ছে, কিন্তু কবির চোখে আর সেই জ্যোতি নেই। তিনি বুঝতে পেরেছেন এবার পৃথিবীকে বিদায় জানিয়ে চলে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। সেজন্যই কি নীচের এই কবিতাটি কিছুদিন আগেই ((১৩ ই মে ১৯৪১) লিখেছিলেন শান্তিনিকেতনে।
প্রথম দিনের সূর্য প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে
কে তুমি ?
মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিম সাগরতীরে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়
কে তুমি ?
পেল না উত্তর ।
কবির উপলব্ধি: সারাটি জীবন চলে গেল, নিজেকেই জানা হোল না। ২৯ জুলাই বিকেলে রানীকে লিখতে বললেন একটি কবিতা। এটিই কবির জীবনের শেষ কবিতা
তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।
……
কিছুতে পারে না তা’রে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভান্ডারে।
৩০ শে জুলাই:
সকাল বেলায় কবিকে দোতলার পাথরের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানেই অস্ত্রোপচারের সব সাজ সরঞ্জাম করা হয়েছে। কবিকে জানানো হল । কবি বিস্মিত। কিছু বললেন না। শুধু সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ রানীকে বললেন, নীচের তিনটি লাইন কালকের বিকেলের কবিতাটার শেষে জুড়ে দিতে –
“অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে,
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার”
বিখ্যাত বিলেতফেরত শল্যচিকিৎসক ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তিন সদস্যের চিকিৎসক দল কবির দেহে অস্ত্রোপচার করলেন। পরিকল্পনামত অস্ত্রোপচার হল ঠিকই কিন্তু কবির শরীরের যন্ত্রণার উপশম হল না। বরং সময়ের সাথে সাথে তা বেড়েই চলল।
৪ অগাস্ট: কবির বৃক্ক (কিডনি ) কাজ করা বন্ধ করে দিল।
৫ অগাস্ট: ইউরেমিয়ায় আক্রান্ত হলেন কবি। ডাঃ নীলরতন সরকার আর ডাঃ বিধান রায় কবিকে দেখতে এলেন সেদিন সকালে। স্যালাইন শুরু হল। নীলরতনবাবু নাড়ি দেখার অছিলায় কবির হাত দুটি ধরে অসহায় দৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন কবির দিকে। তিনি বুঝতে পারলেন কবিকে আর ফেরানো সম্ভব নয়। তারপর নীরবে বিদায় নিলেন। কবিরও চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে দেখা গেল। সে জল ইঙ্গিত দিল –
‘হে বন্ধু বিদায় !’
৬ অগাস্ট:
স্যালাইন চলছে। কবির কোন উন্নতি হয়নি। রাখি পূর্ণিমা – জোড়াসাঁকোর দোতলার ঘরের বারান্দা চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে । কবি আচ্ছন্ন – চাঁদের হাসির ভাঙা বাঁধ আর তাঁর দেখা হল না। পুত্রবধূ প্রতিমাদেবী শান্তিনিকেতন থেকে এলেন বাবা মশাইয়ের কাছে। তিনি চিনতে পারলেন , কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণার জন্য কোনো কথা বললেন না। রাতে অবস্থার দ্রুত অবনতি হল।
৭ অগাস্ট ( ২২শে শ্রাবণ):
সকালে বিধানবাবু আর ললিতবাবু এলেন। কবির নাকের থেকে অক্সিজেন নল খুলে নেওয়া হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কবির শরীরের উষ্ণতা কোথায় মিলিয়ে গেল। পৃথিবীর মানুষকে তিনি দিয়ে গেলেন তাঁর প্রাণের উষ্ণতা আর সঙ্গে নিয়ে গেলেন মানুষের প্রীতির প্রসাদ। নীচ থেকে ভেসে আসছে কারা যেন গাইছে – কে যায় অমৃত পথযাত্রী। বেলা ১২-১০ মিনিটে মর্ত্যলোকের সব বন্ধন ত্যাগ করে কবি পাড়ি দিলেন অমৃতলোকে।
কবি দুটি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন:
এক, তিনি চেয়েছিলেন মৃত্যুর পর তাঁর পার্থিব শরীর যেন শান্তিনিকেতনে খোলা আকাশের নীচে তরুলতা ঘেরা এককোণে শায়িত করা হয়। তিনি তাঁর আশ্রমে ছাত্রছাত্রীদের মাঝেই থাকতে চান। কিন্তু কবির সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। কবিকে পরানো হল সাদা বেনারসীর জোড়, কোঁচানো ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি আর পা পর্যন্ত পাটকরা চাদর। তাঁর কপালে চন্দনের ফোঁটা আর গলায় গোড়ের মালা। রানী বুকের ওপর রাখা কবির হাতে রাখলেন পদ্মের একটি কোরক। লক্ষ লক্ষ মানুষের নীরব চোখের জলের মধ্য দিয়েই লক্ষ হৃদয়ের রাজা রাজবেশে চললেন চিরশান্তির দেশে। নিমতলা মহাশ্মশান ঘাটে কবির শেষকৃত্য সম্পন্ন হল।
দুই, তিনি একটি গান রচনা করেছিলেন ‘ডাকঘর’ নাটকে মঞ্চস্থ করার সময় বালক অমলের মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহের পাশে বসে তাঁর নিজের গলায় গাওয়ার জন্য। ১৯৪০ সালে নাটকের কয়েকপ্রস্ত মহড়াও হয়েছিল। কিন্তু কবি শেষমেষ সিদ্ধান্ত নেন এই গানটি তিনি নাটকে অমলের দাদুর গলায় গাইবেন না। পুত্র রথীন্দ্রনাথকে গানটি দিয়ে বলেন, এটি যেন কবির মৃত্যুর দিন গাওয়া হয়। ১৩৪৮ সালের ২২ শে শ্রাবণ, সন্ধেবেলায় শান্তিনিকেতনে উপাসনা গৃহে গানটি পরিবেশন করেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিদেব ঘোষ সহ কিছু আশ্রমিক। গানটির প্রথম দু লাইন –
“সমুখে শান্তি পারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার”
এই ইচ্ছাটি কবির পূরণ হয়েছিল । তাঁর মুক্তিদাতার সঙ্গে তাঁর মিলন হল এক চিরশান্তির পারাবারের ঘাটে। কবি প্রার্থনা করে তাঁর থেকে পেলেন ক্ষমা আর দয়া। আর সেগুলিকেই পাথেয় করে তিনি শান্তির তরণীতে ভাসতে ভাসতে পৌঁছে গেলেন তাঁর চিরাকাঙ্খিত মুক্তিলোকে।